নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ
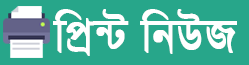
॥ ফারাহ মাসুম ॥
বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এখন উত্তাপ এবং অনিশ্চয়তার মাত্রা বেড়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের আগে ডাকসু-জাকসুর ফল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং আনুপাতিক পদ্ধতি ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ইসলামপন্থী দলগুলোর আন্দোলন নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। পাশাপাশি পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নির্বাচন বানচালে অস্থিরতা ও অন্তর্ঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্বিক পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করছে।
ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের ফল : শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক ব্যারোমিটার : সম্প্রতি ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে দেখা গেছে, দুই শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল বিপুলভাবে জয় পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রলীগ ও বামধারাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও শিক্ষার্থীদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামপন্থী ও স্বতন্ত্র ছাত্র সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন জয় এটি প্রমাণ করছে যে, শিক্ষার্থীরা এখন শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়; তারা জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি প্রভাব
ফেলতে সক্ষম।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ডাকসু-জাকসুর ফল ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগাম সূচক। শিক্ষার্থীদের ভোটের ধারা এবং নির্বাচনী পছন্দ দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং ভোটার মনোভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিজয় তাদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নির্বাচনী চাপ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিজয় ভবিষ্যতের নির্বাচনী কৌশল ও রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত হিসেবে ধরা হচ্ছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ডাকসু-জাকসুর ফল ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের জন্য একটি আগাম ব্যারোমিটার। আসন্ন রাকসু ও চাকসু এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়ও একই ধারা দেখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের ভোটের এ ধারা, নির্বাচনী পছন্দ এবং সমর্থনের প্রভাব সরাসরি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং ভোটার মনোভাব নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।
রাজনৈতিক প্রভাবের মাত্রা : ডাকসু-জাকসুর ফলাফলে দেখাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ ও বাম-সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। বিএনপির ছাত্রশক্তি এর বিকল্প হয়ে উঠতে সমর্থ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলো এখন তাদের ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে ভোটারদের মনোভাব প্রভাবিত করার নতুন উপায় খুঁজছে। অন্যদিকে বিজয়ী ইসলামপন্থী ও স্বাধীন ছাত্র সংগঠনগুলো জাতীয় রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আন্দোলনকে সাধারণ নির্বাচন এবং জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিবার ও সম্প্রদায়ের ভোটারের মনোভাব প্রভাবিত করে। ডাকসু-জাকসুর ফল এ প্রভাবকে প্রমাণ করছে। ফলে সাধারণ নির্বাচনের আগে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে ধরা যায়। শিক্ষার্থীদের সমর্থন যদি তাদের রাজনৈতিক শক্তির জন্য প্রবলভাবে নির্দেশমূলক হয়, তবে তা প্রতিপক্ষ দলের জন্য নির্বাচনী চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবাহও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ডাকসু-জাকসুর ফল প্রমাণ করছে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র আন্দোলনের ধারা এখন জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ভোটাভুটির ফল রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশল, প্রার্থী বাছাই এবং প্রচারণার পদ্ধতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের প্রায় ৫ কোটি ভোটার অনূর্ধ্ব-৩৫ বছরের হওয়ায় এই প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এরা ফ্যাসিবাদের কারণে আগে ভোটদানের সুযোগ পায়নি।
ইসলামপন্থী কৌশল: বিস্তৃত বিশ্লেষণ
গত কয়েক মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো শিক্ষার্থীদের নানা ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন পরিচালনা করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এ আন্দোলনগুলো তিনটি স্তরে পরিচালিত হচ্ছে।
প্রথম স্তরে, আন্দোলনের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের অভ্যন্তরীণ নীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা। এখানে তারা শিক্ষানীতি, ধর্মীয় অধিকার এবং সামাজিক নীতি সংরক্ষণের দাবি তুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমর্থন তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়াবলি বা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাবÑ এগুলো শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল। এ ধরনের আন্দোলন শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপিত করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভোট বা নির্বাচনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ফলে ডাকসু ও জাকসুর নির্বাচনের ফলের মতো পরিস্থিতিতে এ আন্দোলন সরাসরি ফলপ্রসূ হচ্ছে।
দ্বিতীয় স্তরে, আন্দোলনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ধর্মীয় ও যুব সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সাধারণ জনগণ ও সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রভাব বিস্তার করছে। তারা সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় কার্যক্রম এবং জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে জনমত গঠন করছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ স্তরের কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের প্রভাব পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তাদের মনোভাব এবং ভোটের প্রবণতাও প্রভাবিত হচ্ছে।
তৃতীয় স্তরে, আন্দোলনটি সরাসরি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির দিকে নজর দেয়। সাধারণ নির্বাচনের আগে এ আন্দোলন সরকারের নীতি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থিতিশীলতা প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আন্দোলন যে চাপ তৈরি করছে, তা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় ভোটের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। এত বড় দলগুলোর নির্বাচনী কৌশল পুনর্বিন্যস্ত করতে বাধ্য করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের চাপ কৌশলগতভাবে পরিকল্পিত। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার এবং স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করার একটি কৌশল।
এর সামগ্রিক প্রভাব নানামুখী হতে পারে। এতে নির্বাচনী পরিবেশে উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে। আন্দোলন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপের ধারা সৃষ্টি করছে। ভোটার মনোভাব ও ভোটের প্রভাবও এতে স্পষ্ট হতে পারে। শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিবারের ভোটারদের মনোভাবেও প্রভাব ফেলছে। ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনী চাপ তৈরি করে তাদের পক্ষের শক্তিকে রাজনৈতিক সুযোগ দেয়।
সার্বিকভাবে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক নয়; এটি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর যুগপৎ কৌশল একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছে। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব, ভোটার মনোভাব এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর এর প্রভাব যথেষ্ট গভীর হতে পারে।
জামায়াত ও ইসলামী দলের পিআর নির্বাচন দাবি
বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন সাধারণত সরাসরি ও আংশিক আনুপাতিক পদ্ধতিতে হয়। বড়-ছোট মিলিয়ে ইসলামী দলগুলো নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখে; বিশেষ করে ধর্মীয় ও প্রথাগত ভোটারদের মধ্যে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় ছোট দলগুলোও আসন পেতে পারে, তাই জামায়াত ও অন্যরা এ পদ্ধতির সুবিধা নিতে পারে।
এক্ষেত্রে দলগুলোর কৌশল হলো ভোট ব্যাংক সক্রিয় করা। ধর্মনিরপেক্ষ ও যুব ভোটারদের সঙ্গে বিভাজন তৈরি। মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালানো। বড় বা ছোট দল নির্বিশেষে তাদের অবস্থান তুলে ধরা। প্রতিপক্ষ বড় দলগুকে চাপ সৃষ্টি করতে বা ভোট ভাগাভাগি নিশ্চিত করতে জোটবদ্ধ কৌশল তৈরি করা।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ইসলামী দলগুলোর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলোÑ স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, নির্বাচনী সংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থা ও যুবনীতি সংস্কার। তারা জুলাই সনদকে সাংবিধানিক আদেশ অথবা গণভোটের মাধ্যমে এখন থেকেই বাস্তবায়ন করতে চায়। সেটি না হলে জুলাই আন্দোলন স্থায়ী কোনো মূল্য জাতীয় রাজনীতিতে রাখতে সক্ষম হবে না। এ আন্দোলন বিএনপির ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসার পর জুলাই সনদ বাস্তবায়ন কৌশলকে চাপের মধ্যে ফেলেছে।
আনুপাতিক নির্বাচনের বিষয়ে বিএনপির অবস্থান একবারেই নেতিবাচক। ঐকমত্য কমিশন সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক ব্যবস্থার নির্বাচন ও নিম্নকক্ষে গতানুগতিক নির্বাচনের কথা বলেছে। বিএনপি এর সাথেও একমত হয়নি। ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধি প্রক্রিয়ায় ছোট ইসলামী দলগুলোও আসন পেতে পারে। ভোট ভাগাভাগি ও জোটের কারণে বড় দলের ভোটের প্রভাব এতে কমে যায়। অন্যদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আন্দোলন দেশে জুলাইয়ের বিপ্লবকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দেবে। ইসলামী দলগুলোর নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে বড় প্রভাব না থাকলেও, আনুপাতিক প্রতিনিধি ও মিডিয়া কৌশলের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলে আংশিক প্রভাব রাখতে সক্ষম। বিশেষ করে স্থানীয় আসনে ও ধর্মীয় ভোটব্যাঙ্কে এ প্রভাব পড়তে পারে।
মূল বিষয় হলো জামায়াত ও অন্য ইসলামী দলগুলোর স্থায়ী ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে। ফলে আনুপাতিক প্রতিনিধি পদ্ধতি ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন মিডিয়ায় ও জনমতে প্রভাব সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচন স্থগিত বা সীমিত করার যে চেষ্টা ফ্যাসিবাদী পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, তা সাধারণ জনগণ ও দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। নির্বাচন বিলম্বের পরিকল্পনা বা সীমাবদ্ধকরণ নির্বাচন কমিশন ও দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিতে চায় নাÑ যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়ে ওয়ান-ইলেভেন ধরনের আরেকটি সরকার ক্ষমতায় বসতে পারে।
এটি ঠিক যে ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ইসলামপন্থী আন্দোলন এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব একত্রিতভাবে রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু হওয়া উত্তেজনা ভোটার মনোভাব এবং নির্বাচনী পরিবেশে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। ডাকসু-জাকসুর ফল প্রমাণ করছে, ছাত্রনেতৃত্বের প্রভাব জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিতে হবেÑ যাতে ভোট আগের মতো কারসাজির না হয়ে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এ পরিস্থিতি সব দলকে কৌশল পুনর্বিন্যস্ত করতে বাধ্য করছে।
ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে বিএনপির কৌশল
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির কৌশল বেশ জটিল এবং বহুমাত্রিক। এটি মূলত তাদের রাজনৈতিক অবস্থান, নির্বাচনী স্বার্থ এবং জনমত প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গির শীর্র্ষে রয়েছে অংশগ্রহণ কৌশল। বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে তারা এতে বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হতে পারলে বিএনপির এখনকার ইতিবাচক পরিবেশ নাও থাকতে পারে। বিএনপি প্রার্থীর তালিকা ও জোট কৌশলের অংশ হিসাবে দলের প্রভাব বলয়ের মুখ্য জোন সংরক্ষণ করতে চায়। এজন্য তারা কিছু শক্তিশালী লোকাল নেতা বা প্রার্থী ধরে রাখে, যারা ঐক্যবদ্ধ ভোটকে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম। ছোট দল ও ইসলামপন্থী কিছু পক্ষকে তাদের জোটে আনার কৌশলও রয়েছে। স্থানীয়ভাবে তাদের কিছু ইসলামপন্থী বা ছোট দল নিয়ে জোট বানানো সম্ভব হলে তাদের বলয়ের ভোট ভাগ হবে না এবং ভারতের সাথে আপসকামী হিসেবে ট্যাগ দুর্বল হবে বলে মনে করা হয়।
বিএনপির প্রচারণা ও জনমত প্রভাবে ফোকাল ইস্যু হিসেবে নেয়া হয় সাধারণত আগের সরকারের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবকে। দলের মিডিয়া কৌশল হলো ডিজিটাল ও সামাজিকমাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুত জনমত তৈরি করা। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজর কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। বিএনপি আগামী নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে- এমন একটি আবহ তৈরি করে প্রশাসনে প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইছে। যেটিতে আঘাত এসেছে ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের ফলাফলে।
আওয়ামী লীগের অস্থিরতা তৈরির কৌশল
ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তারা কোনোভাবেই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হতে দিতে চায় না। এজন্য তাদের আনুকূল্যে অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়া অলিগার্কদের সহায়তায় ভোটের আগে দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টির এক মহাপরিকল্পনা তৈরি করেছে। এর অংশ হিসেবে কয়েক মুহূর্তের ঝটিকা মিছিল করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোর মাধ্যমে সমর্থকদের মধ্যে আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করছে। এরপর তাদের বড় আকারের নাশকতা তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এটি বাস্তবায়নে তারা প্রতিবেশী দেশে নানাভাবে সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে।
আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য হলো ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের চেষ্টা ভণ্ডুল করা। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও অর্থ পাচারের বিচারের চলমান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। পিলখানা হত্যাযজ্ঞকে বিচারের আওতায় আনার চেষ্টাকে ব্যর্থ করা। আর এ লক্ষ্যে নিজেরা সরাসরি দেশে আসতে না পারলেও ওয়ান-ইলেভেন ধরনের একটি পটপরিবর্তনের দিকে দেশকে নিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলোকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে চায় তারা।
সাধারণ নির্বাচনের জন্য চ্যালেঞ্জ
ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ ইতোমধ্যেই উত্তেজনাপূর্ণ। এ উত্তেজনার মূল উৎস হলো আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টি চেষ্টা। সাম্প্রতিক ডাকসু-জাকসু নির্বাচন ও ইসলামিস্টদের যুগপৎ আন্দোলনও এতে কিছু মাত্রা যুক্ত করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ আন্দোলনগুলো জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তবে ইসলামিস্টরা ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টির পরিবেশ তৈরির ফাঁদের ব্যাপারে বেশ সচেতন বলে মনে হয়।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আগামী নির্বাচনের কয়েকটি চ্যালেঞ্জ নির্দেশ করছেন। এর মধ্যে রয়েছেÑ ভোটার মনোভাব ও অংশগ্রহণে আগ্রহ। শিক্ষার্থী আন্দোলন এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির সংযোগ ভোটারদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করছে এবং ভোটারদের নির্বাচনে আগ্রহকে বৃদ্ধি করেছে। তবে যদি রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ে, তবে ভোটাররা অস্থিরতায় সাড়া দিয়ে ভোটে অংশগ্রহণ কমাতে পারে বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষের প্রতি ঝুঁকতে পারে।
নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও একটি চ্যালেঞ্জ। সাধারণ নির্বাচনের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে ফল নিয়ে বিতর্ক ও অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। এটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করবে। আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিও একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নানা সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রায়ই আইনশৃঙ্খলা হ্রাসের কারণ হতে পারে। নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, তা না হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারের এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভোট প্রক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা। এটি না হলে সাধারণ নির্বাচন শুধুমাত্র ভোটের অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।
ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও যুগপৎ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যারোমিটার হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভোটার মনোভাব, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক, সক্রিয় এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।
ডাকসু-জাকসুর ফল এবং শিক্ষার্থী আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি নতুন ধারা সূচিত করেছে। ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগে এ ধরনের উত্তেজনা এবং অস্থিরতা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভোটের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার মুখে নিয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘোষিত সময়ে নির্বাচন হতে না পারলে তা দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। আর নির্বাচন হতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও স্বচ্ছ। এজন্য নির্বাচনে সমতল সুবিধার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৬:৩৮

